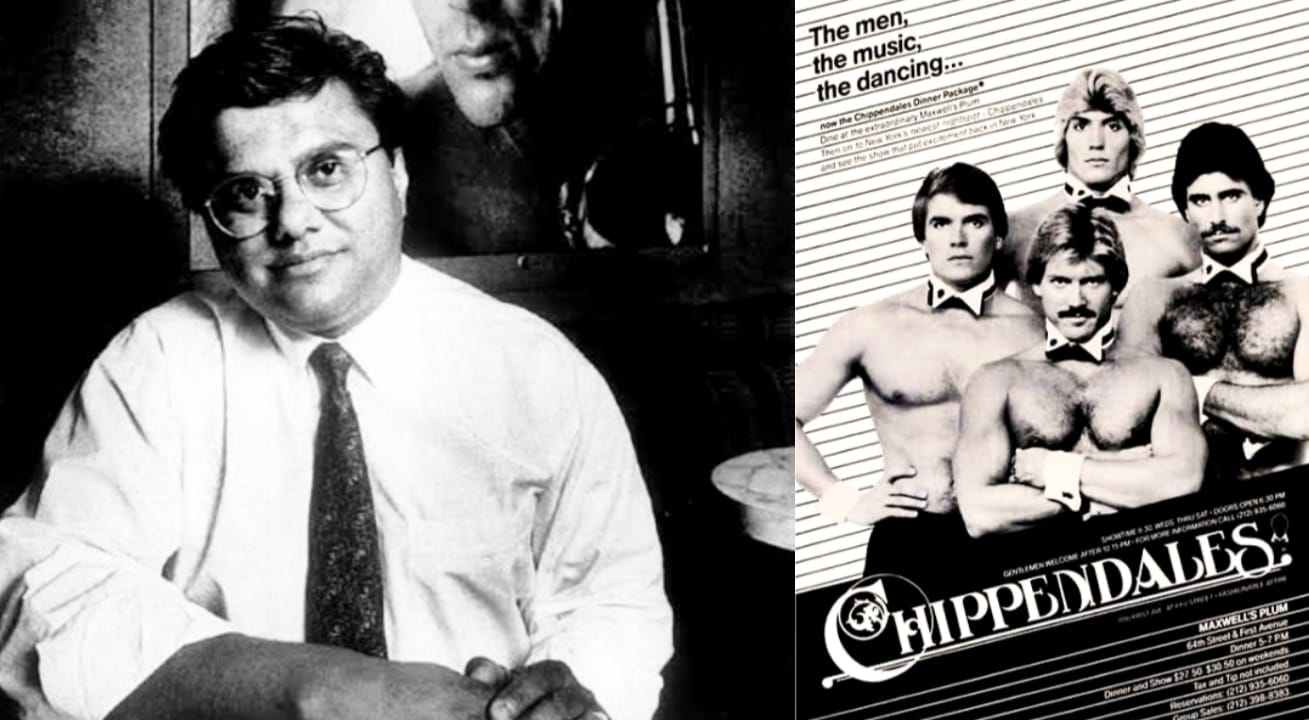চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৫৫ সালে, কলকাতায়। অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষিকা। নব্বইয়ের দশক থেকে সংগ্রহ করছেন পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের গোয়ালপাড়া-শিলচর এলাকার মেয়েদের বিভিন্ন গান। কথা ও সুর সংরক্ষণ করছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। বর্তমান ঈর্ষাক্ষাৎকারটি তাঁর প্রথম বই ‘নারীর গান শ্রমের গান’-কে (প্রকাশসাল ২০২২) কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কথোপকথনে চন্দ্রার সঙ্গী তন্ময় ভট্টাচার্য। আজ দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব...
(প্রথম পর্বের পর)
তন্ময়— কোনো নির্দিষ্ট উৎসব হোক বা দৈনন্দিনের কাজ—বিভিন্ন প্রেক্ষিতে নারীরা গান বেঁধেছেন। এর উদ্দেশ্য কি শুধুই কাজের সময় বিনোদন বা কাজে গতি আনা? নাকি এর পিছনে অন্য কোনো মনস্তত্ত্বও কাজ করে?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— না, গানটা মেয়েরা বাঁধতেন… কাজের গান তো এসেছে—কিন্তু সেই গান বিশেষ কিছু কাজের সময়। যেমন ধান ভানার সময় সুর বা তালটা লাগবে বলে গানটা হয়। কিন্তু আরও অনেক গান আছে—অনেক পুজোর গান আছে, উৎসবের গান আছে—তার মধ্যেও কিন্তু কাজের গান ঢুকে যাচ্ছে। গোড়া থেকে শুরু করি, মেয়েরা কখন গান করেন, কেন গান করেন? ঐতিহাসিকভাবে গোটা পৃথিবীজুড়ে যেটা দেখা গেছে—প্রথমত এটার মধ্যে শিশুপালনের একটা ব্যাপার আছে—ঘুম পাড়ানোর গান সভ্যতার কোন যুগ থেকে শুরু হয়েছে সেটা আমরা জানি না।
আর দ্বিতীয় যে-কথাটা বললাম, মানুষ অন্নের জন্য গান গাইত—খাবারের জন্য, খিদের জন্য গান গাইত। গুহাচিত্রে যখন ছবি আঁকা হচ্ছে, তখন শিকারটা পাব বলেই কিন্তু শিকারের ছবি আঁকা হচ্ছে। এই একটা জাদুবিশ্বাস—যেটা আমি পেতে চাইছি, ছোটো করে সেটার যদি অনুকরণ করি তাহলে আমার সেই জিনিসটা পেতে সুবিধা হবে। কৃষিটা এসেছে তো মেয়েদের হাত ধরে। ফলে যখন থেকে কৃষি শুরু হয়েছে, তখন থেকেই কৃষিভিত্তিক গানও শুরু হয়েছে। এবং সেখানে বৃষ্টি নামানোর জন্য প্রচুর গান করা হয়—প্রচুর রকমের ক্রিয়াকলাপও। এক-এক জেলায় একেকরকম। কোথাও বলা হয় মেঘারানির পুজো, কোথাও বলা হয় মেঘরাজার পুজো, কোথাও বলা হয় হুদোম পুজো, কোথাও মুত্যারানির পুজো, কোথাও কুলো নামানো, কোথাও ব্যাঙ-বিয়া—নানানভাবে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৃষ্টিটা না-হলে আমরা ধানের ভাত খেতে পাব না। পরিষ্কার এই কথাটা বলা হচ্ছে সেখানে। ফলে এই খাদ্য জোগাড় করাটা, খাদ্যের নিশ্চয়তা আনাটা— এটা খানিকটা প্রকৃতির সঙ্গে কথোপকথন, প্রকৃতির কাছে বার্তা পাঠানো যে, তুমি আমাদের সাহায্য করো। প্রকৃতির কাছে এই মাথা নত করা—গানের সুরটা মেঘের কাছে যেতে পারে, গানের সুরটা সূর্যের কাছে যেতে পারে, ধরিত্রীর কাছে যেতে পারে, আমার চাওয়া-পাওয়াটা আমি গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে পারি—এই প্রচলটা কিন্তু হাজার হাজার বছরের। মেয়েরা গান গাইছেন কিন্তু সেই কারণে। বাঁচার প্রয়োজনে। এই গান বিনোদনের নয়। এই গানের কোনো শ্রোতা নেই। এখানে সবাই মিলে গান গাওয়াটাই যেন কর্তব্য। সেটা সমাজ মঙ্গলের সঙ্গে জড়িত। মেয়েদের গান কাউকে শোনানোর গান নয়। এটা একদম আলাদা ব্যাপার। প্রেজেন্টেশনাল মিউজিক বলতে আমরা যা বোঝাই, নানান ঢাক-ঢোল বা বাজনা তার সহযোগে বাজবে—এই গান কিন্তু সেই গান নয়। এখানে গানের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কিছু সময়ে তালবাদ্য থাকে। হারমোনিয়াম বা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকেই না। সবাই মিলে হাতে তালি দিয়ে অথবা অথবা নাচতে নাচতে এই গান গাওয়া হয়।
তো মেয়েদের গান হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনে গান। এবং সেই জীবনের একটা অঙ্গ যেহেতু কাজ, তাই কাজের জন্য গান, কাজের সঙ্গে গান, কখনো কখনো কাজের ভালোলাগা, মন্দলাগা নিয়ে কাজের পরে গান—কাজ করতে গিয়ে কী কী অসুবিধা হচ্ছে, শাক তুলতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটছে, কোথাও বাঘে হুংকার দিচ্ছে, কোথাও কোনো দুষ্ট মানুষ এসে তার সঙ্গে অসভ্যতা করছে—এই সবটাই তারা গানের মধ্যে দিয়ে বলে। গানটা তাদের আত্মপ্রকাশের একটা জায়গা। এবং এই যে তাঁরা প্রকাশ করে দিলেন, তারপর তা কিন্তু সবার হয়ে গেল। ফলে গানটা তাঁদের একটা সোশ্যাল বন্ডিং-এর জায়গা। জেন্ডার বন্ডিং-এর।
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: সুপ্রিয় চৌধুরী — প্রথম পর্ব
তন্ময়— ঠিকই। এই গানগুলো এক অর্থে সমাজদর্পণও হয়ে উঠছে। পড়তে গিয়ে দেখছিলাম, শুধুমাত্র কাজ নয়, তার কাজের পরিচয়টুকু বাদ দিলেও সেই সময়কার সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ, তার চারপাশের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠছে এইসব গান।
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— সব, সব, সবকিছু আছে এই গানে। ওই যে বললাম, যদি সমাজ-ইতিহাসকে আমি জানতে চাই, যদি বাংলা ভাষা কতটা সমৃদ্ধ সেটা জানতে চাই, যদি নারীর ইতিহাস জানতে চাই, যদি জীবন ইতিহাস জানতে চাই—তাহলেও কিন্তু এই গানগুলো সমাজের কাছে মুখ্য আকর। এর মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক কিছু পাব।
তন্ময়— আরও একটা প্রশ্ন। আপনার কথার সূত্রেই আমার মনে হল। স্থানভেদে তো গান বদলে যায়। এবং গানের মধ্যে ভূগোলও ঢুকে পড়ে। জলপাইগুড়ির নারী যে-গান বাঁধবেন এবং বাঁকুড়ার একজন নারী যে-গান বাঁধবেন, তার পটভূমি যদি এক হয়ও, উপস্থাপনা প্রায়শই আলাদা হয়ে যায়। নারীর গানের ভূগোল কীভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা যেতে পারে?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— এটা যদি আমি গেয়ে বোঝাতে পারতাম, তাহলে ভালো হত। জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের কথা ধরুন। এগুলো তরাই অঞ্চল তো, সেখানে সুরের চলন একরকম। আবার পূর্ববঙ্গ যেহেতু অনেক বেশি নদী-নালার দেশ, সেখানে সুরের চলন আরেকরকম। আবার আমি যখন পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে আসছি, সেখানে আবার সুরের চলন অন্যরকম। এবং জীবনটাও যেহেতু সেই অনুযায়ী হয়—যেখানে নদীর জল খুব সহজে পাওয়া যায়, সেখানে জল আনতে যাওয়ার একরকম সুর হবে, একরকম কথা হবে। আবার আমি যখন জল নিতে যাওয়ার গান পুরুলিয়ায় গিয়ে পাচ্ছি, তখন সেখানে তাঁরা বলছেন যে টাকা না-দিলে আমরা জলের কলসি নামাবই না। অর্থাৎ জলটা সেখানে এতটাই মূল্যবান জিনিস যে, জল এনেছি বটে কিন্তু টাকা না-দিলে তা পাওয়া যাবে না। তো এই যে জীবনযাপন, সেই যাপনটাও কিন্তু পুরোপুরি ধরা দেয়, তার সমস্ত রং নিয়ে, তার সমস্ত বৈচিত্র নিয়ে ধরা দেয় এই গানের মধ্যে।
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: সুপ্রিয় চৌধুরী — দ্বিতীয় পর্ব
তন্ময়— এইসব গানের রচনাকাল সন্ধান করা খুবই দুরূহ। কিছু কিছু ছড়ার ক্ষেত্রে যেমন রচনাকালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন— ‘বর্গি এল দেশে’ ইত্যাদি। তার মানে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্ম সে-ছড়ার। আপনার এখানে একটা গানে ‘ইংরেজদের বজরা ঘাটে এসেছে’— এরকম কিছু কিছু প্রসঙ্গ আছে। এসব আপাত রচনাকাল আন্দাজ করা যায়। আপনার দীর্ঘ গবেষণায় কি লোক-পরম্পরা বাহিত গান হিসাবেই এগুলোকে গ্রহণ করেছেন নাকি তার রচনাকাল বা উৎস অনুসন্ধানের দিকেও এগিয়েছেন?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— আসলে এগুলো লোক-পরম্পরার গানই বটে। কিন্তু লোক-পরম্পরার যেটা বীজ, সেটা লিখিত সাহিত্য থেকে আলাদা। যাঁরা লোক-পরম্পরা নিয়ে কাজ করেছেন বা মৌখিক সাহিত্য নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের একটা বক্তব্য আছে। সেটা হচ্ছে, একটা খাগের কলম এসে পৃথিবীটাকে সীমিত করে দিল। অর্থাৎ, একটা লেখা হয়ে গেলে বদলানো মুশকিল। কিন্তু মৌখিক ঐতিহ্য তো তা নয়। সে যেমন পরম্পরাকে ধরে রাখে, তেমন নতুন-নতুন যা কিছু হবে, তাকে যোগও করে তার সঙ্গে। ফলে এখানে কিছু গান হয়তো আসছে যেগুলো পরম্পরা ধরেই চলছে। আবার কিছু কিছু গানে এমন ইঙ্গিত আছে—ধরুন প্রথম ট্রেন এল যখন, তখন ট্রেনকে নিয়ে গান বাঁধছে ‘মনমোহিনী মহারানি রেল কইরাছে খাড়া’— অর্থাৎ সেখানে ভিক্টোরিয়ার কথা বলা হচ্ছে। সেইটা কিন্তু আমি চিহ্নিত করতে পারি যে সেটা কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে। আবার এমন বহু গান আছে, যেগুলো স্বদেশি আন্দোলনের গান বলে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, ‘দেশি সাজন চমৎকার/ পরো বন্ধু একবার/ বিলাতিতে মন দিও না’। অর্থাৎ বিলাতি বর্জন এবং স্বদেশি জিনিস গ্রহণ— সেটা কিন্তু গানের মধ্যে এসে যাচ্ছে। চাল ঝাড়ার গানের মধ্যেও বন্দে মাতরম এসে যাচ্ছে। ‘পাটিতে ঢালিয়া চাল/ চাউল করে আলঝাল/ সবে বলে বন্দে মাতরম’—এ তো পরিষ্কার ধরা যায়। আবার একটা গানে পাচ্ছি, যেখানে বিকেলবেলায় গা-ধুতে যাচ্ছেন, সেখানে বলছেন যে, ‘চলো আমরা জারফানি তুলি/ এই দেশের বাবুরা জারফানি সব তুলে না/ জারফানিতে দ্যাশ রাখল না’ আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। এবার বিভিন্ন আঞ্চলিক অভিধান ঘেঁটে ঘেঁটে দেখা গেল এবং পড়াশোনা করে জানা গেল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই নাকি কচুরিপানার উৎপাত বেড়েছে। এবং মনে করা হচ্ছে জার্মানরা নাকি বিভিন্ন জায়গায় চাল-গম ইত্যাদি তাদের সৈন্যদের জন্য পাঠাচ্ছিল, সেই সঙ্গে কচুরিপানা আমাদের দেশে এসেছে। তার আগে নাকি কচুরিপানা আমাদের দেশের ছিল না। ফলে, এই যে-কচুরিপানা, তার নামই হয়ে গেল জারফানি। তখন আকাশে-বাতাসে কথা ঘুরছে যে, ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ হচ্ছে। ওই যে-শব্দটা পেয়েছে তারা সেখান থেকে, সেটাকেই গান ঢুকিয়ে দিয়েছে তারা— ‘জারফানিতে দ্যাশ রাখল না’। তো এটা থেকে বোঝা যায় এটা কোন সময়ে বাঁধা হয়েছে। আবার উড়োজাহাজ দেখে যখন গান বাঁধছে, সেখান থেকে বোঝা যায় যে তখন ওটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। আপনি, আমি—আমরা তো মেট্রোরেল চড়ি, কিন্তু গান বাঁধি না। কিন্তু মেট্রোরেল নিয়ে যদি কেউ গান বাঁধেন, তাহলে বোঝা যাবে এটা এই সময়ের গান।
তো ব্যাপারগুলো এইরকম, যে সবটা হয়তো ধরা যায় না। আবার কিছু কিছু জিনিস, কিছু কিছু ইঙ্গিত থেকে ধরাও যায়। ধরুন, সাবান তো চিরকাল ছিল না। তার আগে কী ব্যবহার হত? আমি এখানে তো পাচ্ছি সেটাও। ‘ছ্যাঁকাপড়া’ বলা হয় এটাকে। কলাগাছের বাঁশনাগুলোকে সিদ্ধ করে ক্ষার তৈরি করে মাথা ঘষাও হত, আবার কাপড় কাচাও হত। আবার ছ্যাঁকা দিয়ে একরকমের রান্নাও হত। সেটা বিশেষত উত্তরবঙ্গের জিনিস। তো সাবান-পূর্ববর্তী অবস্থাটা এইরকম ছিল। আবার যখন সাবান এসে গেছে, তখন সাবানের কথাই বলা হয়েছে। এইরকম বেশ কিছু ইতিহাসের জিনিসও এখান থেকে উঠে আসে। আমার কাছে একটি গান আছে, সেটা নিয়ে পরে কোনো সময় লিখব—দেশে যখন প্রথম কেরোসিন এল, কেরোসিন তো ছিল না, তা নিয়ে। সেটা প্রায় একশো বছর আগেকার গান। তো এইরকমভাবে একটু টেক্সট পড়া যায়। মানে একটুখানিই পড়া যায়, সবটা পড়া যায় না।
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: বিশ্বজিৎ রায় — প্রথম পর্ব
তন্ময়— এই জাতীয় আঞ্চলিক গান প্রজন্মের সঙ্গে-সঙ্গে লোকমুখে বদলে যায়। নতুন নতুন শব্দ যোগ হয় আধুনিকতর, তার প্রেক্ষিত বদলে যায়, কাঠামোগত মূল অবয়বটা হয়তো এক থাকে, কিন্তু ভেতরের অন্তর্নিহিত শব্দগুলো বদলে যায়। কাজেই এই পথ বেয়ে বা পরবর্তী এই বদলের সামনে দাঁড়িয়ে মূল গানে পৌঁছানোর উপায় কী? আপনি কি মূলের অনুসন্ধানে এগিয়েছেন নাকি পরিবর্তিত রূপটিকেই আরেকটি দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— আমার যেটা ক্ষেত্র, সেটা খুব একটা পরিবর্তনের নয়। খুব বড়ো কোনো পরিবর্তন এখনো পর্যন্ত সেখানে হাত বাড়ায়নি। ফলে আমার ক্ষেত্রে এটা—পুরনো এবং নতুন—যে-দুটো ভার্সানের কথা বলছে, সেটা প্রযোজ্য নয়। মূলত এগুলো পরম্পরাগতভাবে যেভাবেই ছিল, সেভাবেই এসেছে, সেভাবেই রয়েছে। এবং কিছু কিছু জায়গায়, যেখানে আমি শহরের প্রভাব পাচ্ছি, সেটা কিন্তু সেভাবেই গ্রহণ করা ভালো। এটা কিন্তু ওঁরাই পরিবর্তন করছেন, বাইরের কারোর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পরিবর্তন হয়েছে, এমনটা নয়। যে-গানটার সুরটা ওঁদের কোনোভাবে ভালো লেগেছে, সেটাকে ওঁরা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার মূলটা কী ছিল সেটা অন্য কথা, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন একটা গান হচ্ছে। কারণ, মূল গান কিন্তু মূল গানের মতোই আছে। পরবর্তীতে যেটা যোগ হচ্ছে, সেগুলোও স্বতন্ত্রভাবে আছে। এই যে মেট্রোরেল নিয়ে গান গাইছে, সেটার কিন্তু সুরের কাঠামো এবং সবটাই এক, সেখানে কোনো পরিবর্তন নেই। তাও তাঁরা মেট্রোরেল কথাটাও বলছেন না। তাঁরা বলছেন, ‘ভুঁই-এর পরে রেল চালু হল’। তাঁরা তাঁদের মতো করেই বলছেন ব্যাপারটা। এখানে কিন্তু ভেজাল জিনিস এখনো পর্যন্ত সেভাবে ঢুকতে দেখিনি।
তন্ময়— আমি বিশেষ করে শ্রমের গানের দিকেই ভাবতে চাইছি। শ্রমের গান তো একটা প্রজন্ম বা পরম্পরা বাহিত হয়ে আসছে। সেইসঙ্গে এই একুশ শতকে দাঁড়িয়েও কি নতুন গান রচিত হয়? আপনি সেরকম কিছু পেয়েছেন?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— হ্যাঁ। হয় তো। একুশ শতকে এসেও নতুন গান হচ্ছে। বিশ শতকেও নতুন গান হয়েছে। জীবনে যখনই ধরুন নতুন কিছু জিনিস হচ্ছে...
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: বিশ্বজিৎ রায় — দ্বিতীয় পর্ব
তন্ময়— আপনি যেটা বললেন যে, মোবাইল ঢুকে পড়ছে, সবাই নিজের মতো ব্যস্ত, এরকম একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও কি নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গান তৈরি হয়ে চলেছে?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— পুরনো যে-সব মানুষ এখনো অবধি আছেন, তাঁরা নতুন গান তৈরি করছেন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম যখন গানের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন, তাঁরা তখন আর গান করছেনই না। যেমন ধরুন, আমি বিশ শতকেরও একটা গানের কথা আমি বলতে পারি—রেললাইন পাতার জন্য ছোটোনাগপুর থেকে, জঙ্গলমহল থেকে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন এখানে, তখন কিন্তু এমন গান হচ্ছে—নারী গান বাঁধছেন তাঁর স্বামীর জন্য, যে, তুমি হঠাৎ কোমরে ব্যথা পেলে কি? হেলে হেলে হাঁটছ কেন? বলছে, ‘মাটির ঝুড়ি তুলতে গিয়ে লাগিল কোমরে’— এই যে কাজটা করতে গিয়ে তিনি আহত হচ্ছেন, সেটাকে কিন্তু ট্র্যাডিশনাল গানের মধ্যেই বলছে। নতুনকেও তাঁরা কিন্তু তাঁদের মতো করেই গ্রহণ করছেন। সেটা একুশ শতকে এসে কিন্তু মোবাইল নিয়েও গান বাঁধছেন। আমাকে দু’জন বলেছেন যে দিদি মোবাইলের গানও তৈরি হয়েছে। তাঁরা যা দেখছেন, তা নিয়েই গান বাঁধার চেষ্টা করছেন, তাঁরা গানের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছেন।
আমি গল্প শুনেছি, জয়দা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে টুসু ভাসান দেওয়ার একটা বড়ো মেলা হয়। সেখানে গিয়ে টুসুটা ভাসান দেবে ভেবেছিল ছোটো মেয়েরা। কিন্তু টিকিট কাউন্টার খোলেনি বলে ওরা ট্রেনটায় উঠতে পারল না। ট্রেন বেরিয়ে গেল। সেখানে বলছে, ‘টিকিটবাবু টিকিট দিল না/ টুসুর আমার জয়দা যাওয়া হইল না।’ গানটা কিন্তু সেই মুহূর্তেই তৈরি হচ্ছে। আবার ধরুন, কোনো গ্রামে এখনও ইলেকট্রিসিটি আসেনি, ‘তোরা টানাই দেলো বিজলি তার/ করকটা টা বড়ো অন্ধকার’—সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তৈরি হচ্ছে। এই গান তৈরির যে-কৌশল, সেটা তাঁদের ভেতরে এমনভাবে রয়েছে যে কথা বলার মতো করেই তাঁরা কিন্তু গান তৈরি করেন। যেটা আমরা পারব না। আমাদের সৃজনক্ষমতা এতটাই কম এবং ওঁরা যেহেতু এই মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যেই বড়ো হয়েছেন, ফলে গান বাঁধাটা ওঁদের কাছে আলাদা করে কোনো কাজ নয়। আমরা যেমন কথা বলি, সেরকমই।
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: অলোক সরকার — প্রথম পর্ব
তন্ময়— এইসব গানের সূত্র ধরে বিভিন্ন বৈচিত্রময় পেশার কথা উঠে এসেছে। যেগুলোর সম্পর্কে হয়তো আমাদের নগরকেন্দ্রিক জীবন হয়তো জানতেও পারে না, এমন হয়তো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব কাজ। আবার হয়তো এমন কোনো কাজ আছে, যা গ্রামাঞ্চলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গান খোঁজার সূত্র ধরে আপনি এইধরনের হারিয়ে যাওয়া কিছু পেশারও কি সম্মুখীন হয়েছেন?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সম্মুখীন তো হয়েছিই। এই যে ধান ভানার গান—এ তো অনেক আছে। এখানে তো আমি কিছু দিয়েছি, সব দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঢেঁকি উঠে গেছে প্রায়। ঢেঁকি অবলুপ্ত। কিন্তু ঢেঁকির গানগুলো তো আছে। কাজটা লুপ্ত। এমন অনেক জিনিসই আছে, যেগুলো আগে করা হত, কিন্তু এখন আর হয় না। এখন তো মেশিনে মুড়ি ভাজা হয়। মেশিন এসে গেছে। তো এই যে কাজগুলো ছিল, পেশাগুলো ছিল— সেগুলো তো নেই এখন আর।
তন্ময়— কিংবা প্রসবকালীন যে-গানগুলো ছিল…
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— ঠিক। এখন তো হাসপাতালে গিয়ে প্রসব হয়, দাই-মায়েরা আর নেই। ফলে প্রসবকালীন গান উঠে যাচ্ছে, মুড়ি ভাজার গান উঠে যাচ্ছে, ঢেঁকির গান উঠে যাচ্ছে। আরও যেটা উঠে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কাটুনিদের গান। একটা সময় একটা জেলাতে কাটুনি হিসাবে কাজ করতেন ১ লক্ষ ২৫ হাজার মহিলা। যখন আমাদের বস্ত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ ছিল। পুরো বিশ্বে বাংলার কাপড় রপ্তানি হত। কাটুনিরাই তো সুতোটা তৈরি করতেন। তাঁদের তখন এত চাহিদা…
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: অলোক সরকার — দ্বিতীয় পর্ব
তন্ময়— এটা কোথাকার কথা বলছেন?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— নদিয়ার শান্তিপুর যেমন একটা কেন্দ্র ছিল, পূর্ববঙ্গের ঢাকাও তেমন একটা কেন্দ্র ছিল। মসলিনের কাজ ঢাকাতেই বেশি হত। ওঁরা লিখছেন যে, এক থেকে কুড়ি—সূক্ষ্মতা হিসাবে এতগুলো ভাগ হত সুতোর। কাটুনি কিন্তু সুতো কাটতে কাটতে, সুতোর ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে দেখে, সূক্ষ্মতা কমে যাচ্ছে দেখে, তাদের আলাদা করে রাখতে পারতেন। এত দক্ষ কাটুনি ছিলেন বাংলায়। সেই কাটুনিদের দিয়ে সুতো কাটানোর জন্য তাঁদের আগে থেকে বায়না করে নিয়ে যাওয়া হত। সুতোর দাম এতটাই বেশি ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, এখন তো সেই কাটুনি আর নেই। বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।
তন্ময়— এই সূত্রে প্রাক-পলাশী যুদ্ধে বাংলার যে বস্ত্রশিল্পের রমরমা তাতে নারীদের অবদানের দিকটাও এই কাটুনিদের প্রেক্ষিতে উঠে আসতে পারে…
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— একদমই তাই। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, এখন আপনি যদি নদীয়ার ফুলিয়াতে যান, দেখবেন চরকা এখনও চলে। কিন্তু চরকায় সুতো কাটা হয় না। সুতো গোটানো হয়। অতি স্বল্প মজুরি তাঁদের। কারণ, ওখানে তো দক্ষতার ব্যাপার নেই কোনো। তাঁতি ঘরের মেয়েরাই এই কাজটা করেন।
তাঁতিদের নিয়ে একটা পত্রিকা বেরোয়, ‘টানাপোড়েন’ তার নাম। ফুলিয়া থেকেই বেরোয়। সেখানে বসাক পরিবারের কয়েকজন আছেন। সেই পত্রিকায় মনোহর বসাকের একটা লেখাই ছিল ‘তাঁত শিল্পে মেয়েরা’। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তাঁতি তাঁতে বসে বোনার কাজটা করেন, কিন্তু তার আগের ধাপগুলো—সেগুলো মেয়েরাই করে। পাশাপাশি আজ মহিলা তাঁতিরাও রয়েছেন। ফলে বস্ত্রশিল্পে মেয়েদের অবদান অনেক। এবং সেটা আজকের নয়। রাধাগোবিন্দ বসাকের লেখা পড়ছি, ‘প্রবাসী’-তে বেরিয়েছিল ১৯৩৫ সালে, সেখানে উনি দেখাচ্ছেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা—মেয়েরা তখনো সুতো কেটে রোজগার করতেন—কেউ রাজসভায় এসে সুতো কেটে যেতেন, যাঁরা আসতে চাইতেন না তাঁদের কাছে সুতো কাটার সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হত, তাঁরা বাড়িতে বসে সুতো কেটে পাঠিয়ে দিতেন। এটা কৌটিল্যের সময়কার ঘটনা। ফলে বস্ত্রশিল্পে মেয়েদের অবদান যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। কারণ, সুতো কাটাটা সূক্ষ্ম ব্যাপার, ধৈর্যের ব্যাপার, হাতটা নরম না-হলে হবে না— তাঁদের চোখ এবং মাথা যাতে ঠান্ডা থাকে তার জন্য রাজকোষ থেকে তাদের জন্য আমলকি, তেল এসব পাঠিয়ে দেওয়া হত। চোখের জ্যোতি যাতে ঠিক থাকে, হাতটা যেন নরম থাকে…
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: স্বপনকুমার ঠাকুর — প্রথম পর্ব
তন্ময়— আপনি যাঁদের থেকে গান উদ্ধার করেছেন, তার মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীরাই আছেন। এইসব কর্মসঙ্গীত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। কিন্তু এমন কি কোনো গান আছে, যেটা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে গান? বা এইসব শ্রমসঙ্গীতকে কি হিন্দু-মুসলমান সমাজের নারীদের ঐক্য হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— আপনি দুটো সম্প্রদায়ের কথা বললেন—হিন্দু এবং মুসলমান। আমরা সাধারণভাবে যাদের তফসিলি জাতি বা উপজাতি বলি—উপজাতিরা ট্রাইব, তাঁরা একদম আলাদা ভাষায় কথা বলেন—কিন্তু যাঁরা তফসিলি জাতি, তাঁরাও তো ঠিক হিন্দু ছিলেন না। এখন অনেকটা হিন্দু হয়েছেন। এখনও সব রিচ্যুয়াল তাঁরা হিন্দুদের মতো মানেন না। ফলে আমার কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে কিন্তু বাউরিরা আছেন, কুড়মিরা আছেন, মাহাতোরা আছেন, শবর আছেন, ভূমিজ আছেন, মাহালিরা আছেন। এঁদের হিন্দুদের মধ্যে মিশিয়ে ফেললে একটু মুশকিল হবে। বাংলায় যত গোষ্ঠী আছে— যাঁরা বাংলা ভাষাটাকে ব্যবহার করেন—আমি উপজাতিদের কথা বলছি না, কারণ আমি তাঁদের কাছে যাইনি কেন-না তাঁদের ভাষাটা আমি বুঝি না, কাজটাকে বেঁধেছি আমি কেবলমাত্র বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে।
দুই, আপনি যেটা বললেন, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের প্রসঙ্গটা… সেখানে কাজের ক্ষেত্রে—ধরুন ধান ভানার কাজ, সে তো হিন্দুরাও করছেন, আবার মুসলিমরাও করছেন, কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে তাঁরা একসঙ্গে করছেন।
তন্ময়— আচ্ছা। তার মানে একই গান গাইছেন, এমনটা নয়?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— একই গানের মতো গান। কিন্তু এক গান নয়। কারণ অঞ্চলটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে। যে-গ্রামটি মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে, সেখানে মুসলমানরাই তো গান গাইবেন, আর যেখানে হিন্দু-প্রধান অঞ্চল সেখানে হিন্দুরা। একই গান, একইসঙ্গে কাজ করছেন—এটা বলা যায় না। কিন্তু আমাদের মাটি-জল-হাওয়া এসবই তো এক। ফলে, কিছু রিচ্যুয়ালসও এক। যেমন, হিন্দুদের মধ্যে যখন বৃদ্ধির ধান ভানা হত—যেটা খাবার ধান নয়, পবিত্র ধান ভানা বলা হত যেটাকে—তার আগে ঢেঁকিকে বরণ করা হয়। ঢেঁকিমঙ্গল বলে এটাকে। মুসলিমদের মধ্যেও এই একই জিনিস আছে, তাঁরা বলেন ঢেঁকিমুঙ্গলানো। এঁদের হবে পানখিলি—বিয়ের আগে যে-পান সাজা হবে সেই অনুষ্ঠান। আর ওঁরা বলেন পানচিনি। এবং মুসলিমদের গানের মধ্যেও কিন্তু শাঁখা-সিঁদুর-আলতা এসবের কথাও উঠে আসে। ফলে, আমরা যে একই সংস্কৃতি থেকে উঠে আসছি— সেইটা কিন্তু এইভাবেই প্রতিফলিত। এবং আমি যে বৃষ্টি আনার গানের কথা বলছিলাম, ‘মুত্যারানি’ বলে, মূর্শিদাবাদ-বর্ধমান অঞ্চলে মূলত যেটা হয়—এই গান হিন্দুদের মধ্যেও আছে, মুসলমানদের মধ্যেও আছে। ফলে, এটা হচ্ছে খানিকটা অঞ্চলভিত্তিক ব্যাপার। এখানে ধর্মীয় বেড়াটা বড়ো কথা নয়। যিনি যে-অঞ্চলে আছেন, তিনি সেই অঞ্চলের গান গাইছেন।
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: স্বপনকুমার ঠাকুর — দ্বিতীয় পর্ব
তন্ময়— উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, নারীর লিখিত সাহিত্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। তুলনায় লিখিত সাহিত্যের জায়গাটা অনেকটাই পুরুষদের করায়ত্ত। সেই জায়গায় নারীদের সাক্ষ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন ব্রতের মন্ত্রের, গানে—সাধারণত মেয়েলি ব্রত যেগুলোকে বলে, তার মধ্যে। এবং এগুলো মুখে মুখে রচিত হলেও এগুলোকে নারীর বয়ান হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে, যেখান থেকে নারীর মনস্তত্ত্ব চেনা যায়। আপনি একটা খুব সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেছেন। ‘অনক্ষর’ নারী। তো, সেই অনক্ষর নারীদের মুখে মুখে ‘লেখা’ এইসব গানের সাহিত্যমূল্য আপনি কীভাবে বিচার করেন?। সমাজমূল্য, ইতিহাসমূল্য এসব সরিয়ে রাখলে, এইসব গানের সাহিত্যমূল্য আপনার চোখে কীরকম?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— আপনি যে-প্রশ্নটা করলেন, তার বাইরে আমি দু-তিনটে কথা বলব। প্রথমত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে যেটা আপনি বলছেন, তখন কিন্তু নারী সাক্ষর হতে শুরু করেছেন। সেই সাক্ষরতা উনিশ শতক ছেড়ে দিয়ে, বিশ শতকের গোড়ার দিকের যে-সেনসাস, ১৯১১ সালের—সেখানে নারী-সাক্ষরতার হার কিন্তু ৪ শতাংশের কাছাকাছি। তার মধ্যে সবাই বই লিখছেন না। বই লিখছেন এবং সেই বই ছাপা হয়েছে—এমন কত জন? যাঁরা সেই পরিবেশটুকু পেয়েছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই। সেটা ১ শতাংশও নয়, আধ শতাংশও নয়। অর্থাৎ বাকি ৯৯ শতাংশের কোনো ইতিহাস নেই।
এবার দ্বিতীয় কথা যেটা। যেটা নিয়ে আমি এখনও যথেষ্ট পড়াশোনা করিনি, তবে কোনো এক সময়ে একটা বইয়ের কাজ করার কথা আছে। এই যে ব্রত নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একটা কাজ করে গেছেন, খুব ভালো কাজ। সেইটাকে ধরে আরও অনেক কাজ চলছে। কিন্তু এই যে ব্রত—এটাকে নারীকণ্ঠ বলতে আমি খুব সায় পাই না। কেন পাই না? কেন-না অবনীন্দ্রনাথই বলছেন, যেসব ব্রত পাই, সেটা অনেকটাই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত। নির্দিষ্ট দিনে অমুক করতে হবে, তমুক করতে হবে… এই যে ব্রতের ব্যাপারগুলো আছে—‘আমি পুজো করি পিটুলির চিরুনির/ আমার যেন হয় সোনার চিরুনি।’ এই চাওয়াটা হয় এই চাওয়াটা একজন ব্যক্তির চাওয়া, এটা কোনো গোষ্ঠীর চাওয়া হতে পারে না। কারণ, আমি যে-মেয়েদের কথা বলছি, তাঁরা কখনো একার জন্য কিচ্ছু চাননি।
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত — প্রথম পর্ব
তন্ময়— ব্রতগুলোর জরুরি একটা বিশ্লেষণ করলেন।
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— এটা নিয়ে পরে কোনো সময়ে আমার ডিটেলে কাজ করবার ইচ্ছে আছে। এবং ব্রতের বেসিক হচ্ছে আমার তিন কুল। অর্থাৎ, আমার বাবার কুল, আমার মায়ের কুল আর আমার শ্বশুরকুল। এঁরা তিনকুলের বেশি কিন্তু যান না। কিন্তু এই যে গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা আমাদের, এখানে আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই মিলে কিন্তু বসবাস করি আমরা। আমি বৃষ্টিটা শুধু আমার কুলের জন্য চাই না। এবং সেখানে এতটাই গভীরতা তাদের দৃষ্টিতে— এমন অনেক গান আছে এমনকি সেটা শুধু মানুষের জন্যেও নয়। আমরা আজকাল যে-ইকোলজির কথা বলি, এটা শুধু মানুষের জন্য নয়, তেমনই। তাঁরা বলছেন, আহা ওই বিড়ালের ছা-টা চ্যাঁও চ্যাঁও করছে, ওই বিড়ালটারও বৃষ্টি দরকার।
তন্ময়— ব্রত নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করে যেটুকু বুঝেছি, ব্রতগুলো অনেকটা ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। আর আপনি যে-নারীগানের কথা বলছেন কিংবা যে-শ্রমের কথা বলছেন, সেটা অনেকটা সামাজিক বা গোষ্ঠীভুক্ত স্বার্থকে সামনে রেখেই বোনা।
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— একদম, ঠিক। এখানে একেবারে যৌথ সমাজ। সেখানে নারীর নামে এক কাঠাও জমি নেই। কিন্তু তিনি যাচ্ছেন বৃষ্টিটা আনাতে…
তন্ময়— সামাজিক স্তরভেদের জন্যই কি এই পরিস্থিতি? কারণ যাঁরা ব্রত করছেন, তাঁরা মূলত সমাজের উচ্চস্তরের...
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— ঠিক। শুধু উচ্চই নয়, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত। ব্রত উদযাপন হবে, তিন বছর ধরে ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে হবে, পুজো দিতে হবে— এইসব ব্যাপার আছে। বলা হয়েছে ‘নির্ধনের ধন হয়, অপুত্রের পুত্র হয়’ ইত্যাদি। শ্রমসঙ্গীতে কিন্তু কন্যাকে কোনোদিন ছোটো করে দেখেনি। বিয়েটাকে জীবনের মুখ্য করে দেখেনি।
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত — দ্বিতীয় পর্ব
তন্ময়— এইখানেই বোধহয় প্রমাণিত হয় আপনার একটু আগে ব্যবহৃত ওই কথাগুলো, যে, গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা অনেক বেশি মুক্তচিন্তক…
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— একদম। এবং আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধা করেই বলছি যে, বিধবা বিবাহ নিয়ে এত লড়ালড়ি, সেটা কিন্তু সমাজের একটা অংশের জন্যেই। অন্য অংশে বিধবা বিবাহ ছিল, আছে, থাকবে। এঁদের যদি ছোটোবেলায় বর মারা যান, তাহলে এঁরা কিন্তু আবার বিয়ে করতে পারেন এবং করেন। এবং অনেক সমাজে সেটা অ্যাক্সেপ্টেড। এবং সন্তান-সহ আরেকজনকে বিয়ে করেন। গান আছে, ‘বিয়াইলা বর, সাঙ্গাইলা বর।’ গানের মধ্যেই বলছেন, সাঙ্গাইলা বরটা বড়ো ছটফটা, বিয়াইলা বরটা ভালো। বিয়াইলা বর যদি থাকত তাহলে আমাকে ছাতার তলায় নিয়ে যেত। সাঙ্গাইলা বরটা ভালো না। বিধবা বিবাহ আছে, বিবাহ বিচ্ছেদ আছে। অত্যাচার বেশি হলে চলে আসে, কারণ সে কাউকে পরোয়া করে না। এমনকি এখানে খোরপোশ দিতে হবে, এই দিতে হবে, ওই দিতে হবে—এসব নেই। কীসের খোরপোশ? যে যার নিজের মতো খাব। রোজগার করব, খাব। এখানে পরনির্ভর নয় মেয়েরা, খোরপোশের ধার ধারেন না তাঁরা।
তন্ময়— অপূর্ব একটা দিক উঠে এল আগের প্রশ্নটার সূত্রে। এবার, সাহিত্যমূল্য...
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— দেখুন, এগুলো তো অনেকটা স্পনটেনিয়াসলি হয়। খুব পরিকল্পিতভাবে একটা কেটে, আরেকটা লিখে—এভাবে তো হয় না। সঙ্গে সঙ্গে হয়। কিন্তু তার মধ্যে রসবোধ এবং সাহিত্যবোধ যথেষ্ট রয়েছে। আমি তো চমকে চমকে গেছি এক একবারে। প্রেমের সম্পর্ককে এইভাবে যদি কেউ দেখে যে, ‘আঙুলে আঙুলে ভাব ছিল’। আপনি ভাবতে পারছেন? নিবিড়তাকে কত সহজ করে কত সুন্দর করে বোঝানো হচ্ছে। সাহিত্যমূল্য যথেষ্ট রয়েছে এইসব গানের। তবে একজন কবির মতো—আমি অবশ্যই সেটা বলব না। এখানে পরিশীলনের জায়গা আছে। সেখানে হয়তো আরও অনেক দিক থাকতে পারে। তবে এদের সহজ কথা, সহজ সুরের যে-সাহিত্য, সহজ সাহিত্য—তার মূল্য বিন্দুমাত্র কম নয়।
আরও পড়ুন : ঈর্ষাক্ষাৎকার: চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় — প্রথম পর্ব
তন্ময়— এবার শেষ প্রশ্ন। আপনি দীর্ঘ এতগুলো দশক ধরে ক্ষেত্রসমীক্ষক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এইসব গান সংগ্রহ করেছেন। এই জাতীয় কাজ করার ক্ষেত্রে, তরুণ প্রজন্মের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়— প্রথমত, কাউকে পরামর্শ দেওয়ার মতো জায়গায় আমি নেই। দ্বিতীয়ত, এখানেও আমি একটু অন্য সুরে কথা বলব। ক্ষেত্রসমীক্ষা কথাটা যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমি কিন্তু সেই অর্থে ব্যবহার করার একেবারেই পক্ষপাতী নই। কে ক্ষেত্র? কে সমীক্ষক? ক্ষেত্র বলতে সে নির্জীব, পড়ে আছে। যদি মন থেকে দরদ দিয়ে যদি কাজ করতে পারি, সেখানে কেউ ক্ষেত্র নয়। আমিও সেই ক্ষেত্রেরই অধীনে। বরং, আমি বাইরে থেকে গিয়ে মাথা নত করে প্রার্থীর মতো জোড়হাতে দাঁড়াব। পরবর্তী প্রজন্মকে বলব, আমার নিজের প্রজন্মকে বলব, সবাইকে বলব আগে ভালোবাসুন, আগে শ্রদ্ধা করুন। এখন ক্ষেত্রসমীক্ষার যে-ব্যাপারটা হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে, আগে কিছু প্রশ্ন করে নিয়ে গিয়ে, তারপর... প্রশ্ন করার মধ্যেই তো একটা আধিপত্য আছে। একটা ছক দিয়ে দেওয়া হয়, এইভাবে প্রশ্ন করতে হবে। আমি কি জানি তাঁদের? জানি না তো। আইকিউ টেস্ট যেমন এখন অনেকেই পছন্দ করেন না। ইমোশন এসে গেছে এখন। ইমোশনাল কোশেন্ট বলা হয়, সেইরকম ক্ষেত্রসমীক্ষার ব্যাপারটা নিয়েও আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে, কে ক্ষেত্র আর কে সমীক্ষা? ওঁরা যদি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন, আমি উত্তর দিতে পারব তার? ফলে, আমাকে একজন অংশী হতে হবে, এই মানুষদের জীবনের একজন অংশী হয়ে উঠতে হবে। বাইরে থেকে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে কাজ করলে, সেই কাজ ভালো ফল দেয় না, সে-কাজে প্রাণ থাকে না। আর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ না-মিললে, স্ট্যাটিস্টিকস হয়তো হয়, কিন্তু এই ধরনের কাজ হয় না।
(সমাপ্ত)
অনুলিখন - শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
অলঙ্করণ - অমর্ত্য খামরুই
Powered by Froala Editor