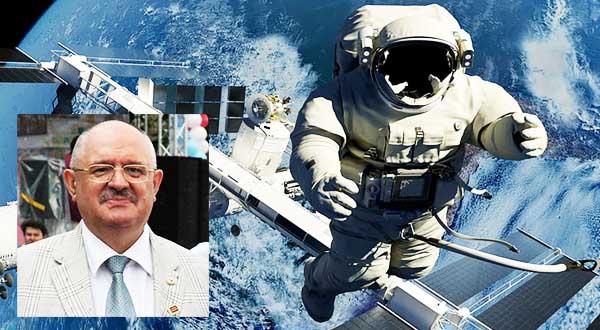১৯১৪ সালে বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ‘চতুরঙ্গ’। অনেকেই হয়তো মনে রেখেছেন জ্যাঠামশাই জগমোহনের কথা। উদার ও ঋজু চরিত্রের মানুষটি মারা যান মর্মান্তিকভাবে। সেই খবর আমাদের জানাচ্ছে শ্রীবিলাস -
‘পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন - ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।’
নিজের উদ্যোগে তখন প্রাইভেট হাসপাতাল খুললেন জগমোহন। শচীশ, শ্রীবিলাস, এরাই ছিল শুশ্রূষার কাজে, সঙ্গে ছিলেন জনৈক ডাক্তারও। যদিও তাদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়নি। শ্রীবিলাসের কথায় -
‘আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম, কোনো খেদ রহিল না।’
দাদার মৃত্যু নিয়ে শচীশের বাবা হরিমোহনের বক্তব্য ছিল অতি সংক্ষিপ্ত – ‘নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।’
ফিরে ফিরেই বাংলা সাহিত্যে এসেছে মহামারীর উল্লেখ। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষে আর যারই অভাব থাক; প্লেগ-কলেরা বা বসন্ত রোগের কোনো কমতি ছিল না। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর জল-বাতাস ও অপর্যাপ্ত চিকিৎসার জেরে প্রাণ হারাতে হত অনেককেই। আমাদের লেখকেরাও ভুলে যাননি, সাহিত্য সমাজের সামনে একটি আয়না ধরে রাখতে দায়বদ্ধ।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। এর দ্বিতীয় পর্ব বেরিয়েছিল ১৯১৮ সালে। রাজলক্ষীর থেকে বিদায় নিয়ে বর্মা দেশে (আজকের মায়ানমার) যাচ্ছে শ্রীকান্ত। কলকাতার জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখে, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোদ্দো পনেরোশো মানুষ। কৌতূহল বশে সে শুধোয় তাদের একজনকে। কথাবার্তাটুকু নিচে রইল -
‘একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ তো সকালে বসেছিলে – হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?
সে কহিল, ডগদরি হোগা?
ডগদরি পদার্থটি কি বাপু?
লোকটি পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগকা ডগদরি।’
এই ‘পিলেগ’ যে আসলে প্লেগ, তা তখনও বোঝেনি শ্রীকান্ত। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য সে আরো খোঁজখবর করে জানে, ‘বর্মায় এখনও প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে।’
প্লেগের পরীক্ষা কেমন? তাও প্রত্যক্ষ করে শ্রীকান্ত –
‘সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থান বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তারসাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার-চিত্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা।’
জাহাজ যেদিন রেঙ্গুন পৌঁছবে, সেদিনই সকালে শ্রীকান্ত দেখে, সমস্ত লোকের মুখে ভয় ও চাঞ্চল্য। চারদিক থেকে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসছে –
‘কেরেন্টিন – কেরেন্টিন।’
কেরেন্টিন-এর মানে হচ্ছে ‘কোয়ারেন্টাইন’। রেঙ্গুন সরকারের নিয়ম অনুসারে নতুনদের কিছুদিন কোয়ারেন্টাইন-এ থাকতে হয়, যদিও সে আইন কুলিদের জন্যেই – ভদ্রলোকের জন্য নয়। ‘যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশি দেয় নাই, সেই কুলি।’ জনৈক ডাক্তার শ্রীকান্তকে জানান, ‘Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না।’
মহামারীর আরেক বিশ্বস্ত ছবি পাওয়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে। ‘আরণ্যক’ (১৯৩৯) উপন্যাসে নায়ক সত্যচরণের মুখে সেই বিবরণ শুনি আমরা।
‘সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল, কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই।’
কাছারির কিছু লোককে সঙ্গী করে সত্যচরণ সেই বস্তিতে যায়, ভেবেছিল, ‘এইসব ডাক্তার-কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি।’ সেখানে রাজু পাঁড়েও উপস্থিত ছিল, সে সত্যচরণকে বাড়িগুলি ঘুরিয়ে দেখায়। সত্যচরণের কথায়,
‘কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মূর্তি কুটিরে কুটিরে। সবই খোলার কিংবা খড়ের বাড়ি, ছোট্ট ছোট্ট ঘর, জানালা নাই, আলো-বাতাস ঢোকে না কোনো ঘরে। প্রায় সব ঘরেই দু-একটি রোগী, ঘরের মেঝেতে ময়লা বিছানায় শুইয়া। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, পথ্য নাই।’
মুমূর্ষু স্বামীকে দেখবার কেউই নেই স্ত্রী ছাড়া। সেই কুটিরে গেছে সত্যচরণ। রোগীর তখন শেষ অবস্থা, শয্যার পাশে তার স্ত্রী। এমন সময় সত্যচরণের চোখে পড়ে -
‘তাকের উপর একটা আঢাকা পাথরের খোরায় দুটি পান্তা ভাত। ভাতের উপর দু-দশটা মাছি বসিয়া আছে। কি সর্বনাশ! ভীষণ এশিয়াটিক কলেরার রোগী ঘরে, আর রোগীর নিকট হইতে তিন হাতের মধ্যে ঢাকাবিহীন খোরায় ভাত।’
গ্রাম্য স্ত্রীলোকের খাদ্য সেই ভাতই। সত্যচরণ তাকে বলে, ‘যাও, এখুনি ফেলে আসো’। স্ত্রীলোকটি ভয়ে ভয়ে তা ফেলেও আসে। আরো কিছু বাড়িতে ঘুরে সত্যচরণ বুঝতে পারে, এখানে সংক্রামক রোগ ঠেকানো প্রায় অসম্ভব। ভাগ্যে যার মৃত্যু আছে, তার হবেই। সেই মুমূর্ষু স্বামীটি তো আগেই মারা গেছিল, তার বউটিও একদিন মারা যায়। খবর শুনে নিজের আক্ষেপ জানাচ্ছে সে -
‘আমার মনে কষ্ট রহিয়া গেল যে, আমি তাহাকে তাহার মুখের অত সাধের ভাত দুটি খাইতে দিই নাই। ’
‘গণদেবতা’ উপন্যাসে কলেরার বিস্তৃত উল্লেখ রেখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নায়ক দেবনাথ যুবক সঙ্গীদের নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিল গ্রামে ছড়িয়ে-পড়া কলেরা রুখতে। তার ছোটো ছেলেকেও ধরেছিল সংক্রমণ, সে-খবর দেবনাথ পায় প্রতিবেশিনী দুর্গার কাছে। লেখক জানাচ্ছেন –
‘হ্যাঁ, দুর্গাই। অন্ধকার পথের উপর আলো হাতে দুর্গাই দাঁড়াইল।
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দুর্গা বলিল – ‘হ্যাঁ, বাড়ী এস শীগগির। খোকার অসুখ করেছে, একেবারে জলের মতন’-
দেবু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একলাফে পথে নামিয়া ডাকিল - ‘ডাক্তার!’
শুধু খোকা নয়, কলেরায় মারা যায় খোকার মা বিলুও। ‘দেবু পাথরের মত অশ্রুহীন নেত্রে নীরব নির্বাক হইয়া সব দেখিল – বুক পাতিয়া নিদারুণ আঘাত গ্রহণ করিল। …বিলুর সৎকার যখন শেষ হইল, তখন সূর্যোদয় হইতেছে।’
শশী ডাক্তারকে মনে পড়ে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র নায়ক শশী চেয়েছিল নিজের গ্রামেই থেকে যেতে, দুঃখী মানুষগুলির কাজে লাগতে। গাওদিয়া গ্রামের প্রকৃতি ছিল নিষ্করুণ, অন্যতম বিপদ ছিল মহামারী। প্রায়ই ছড়িয়ে পড়ত কলেরা, টাইফয়েড, কালাজ্বর ও বসন্তের মতো ব্যাধিগুলি। শশী তার সাধ্যের সীমা অবধি চেষ্টা করেছিল, কাউকে কাউকে সারিয়েও তুলেছিল – কিন্তু কতদূর তার পক্ষে সম্ভব?
গ্রামের মানুষগুলি ডুবে ছিল অশিক্ষায়, কুসংস্কারে। স্বাস্থ্যবিধির কোনো নিয়মই তারা জানত না, জানালেও পালন করা খুব সহজ হত না। গাওদিয়া-র বর্ষা বা বসন্ত ঋতু তাই বড় সুন্দর ছিল না। নিরাবেগ লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর্দ্র-কর্দমাক্ত পল্লীকে দেখেছেন জীবাণুর তীর্থ হিসেবে; শশী ডাক্তারের কাছে ‘গাওদিয়া’ ছিল অনন্ত নরক-পর্যটন।
অতীত বাংলা সাহিত্য থেকে এমন উদাহরণ দেওয়া অনেকই। যদিও আশার কথা, অভিশাপের দিনগুলি চিরস্থায়ী হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে দারিদ্র্য কমেনি, পরিবেশও যে স্বাস্থ্যের খুব অনুকূল - তা বলা যায় না। তবু চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু দান তো থেকেই গেছে। প্লেগ বা কলেরা নামগুলি আগের মতো ততখানি আতঙ্ক ছড়ায় না আর, এগুলি আজকের দিনে নিরাময়-যোগ্য। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যও কি সেই আতঙ্ক থেকে মুক্ত?
উত্তর হবে, ‘না’। বাঙালি লেখকেরা বারে বারেই ফিরে গেছেন সংক্রামক অসুখের কাছে। বাস্তব বিবরণই শুধু নয়, দরকারে কল্প-জগৎ তৈরি ক’রে নিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যায় ১৯৯৯ সালে ‘আজকাল’ পত্রিকার তরফে প্রকাশিত একটি লেখা।
‘ভারতবর্ষ’ নামে এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি লেখেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। দুটি ভিন্ন ধর্মের নারী-পুরুষের প্রেমের আখ্যান, তারই সমান্তরালে রাখা হয় ১০০ বছর পরের ভারতবর্ষের ‘কাল্পনিক’ বিবরণ। এক অজানা মড়কে তখন উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল দেশ, নরনারীরা মিলিত হচ্ছিল যত্রতত্র। মিলনের দ্বারা রোগ ছড়িয়ে-পড়া আটকানো সম্ভব, এমনটাই ছিল নিদান।
বোঝাই যাচ্ছে, লেখাটা সর্বার্থেই ছিল প্রতীকী। বাবরি মসজিদ কাণ্ড (১৯৯২) ও তার পরবর্তী দাঙ্গা ছিল বাস্তব কালপর্ব। হিন্দু রমণী ও মুসলমান পুরুষটির প্রেম ছিল অবৈধ, সমাজ তা স্বীকার করবে না। ২১০০ সালের ভারতে কিন্তু দেখা গেছিল অন্য চিত্র, উন্মত্ত মিলনই সেখানকার দৈনিক সত্য। ভয়াবহ মড়কে মানুষগুলি মরছিল শয়ে শয়ে। মড়ক কেটে গেলে সেই ধ্বস্ত দেশে একটি নতুন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। রক্তমাংসময় এক হিংস্র কুকুর ছিল দেশের সম্রাট। দ্বিপদ জনতা তাকেই সম্মান ও অনুকরণ করত। অন্তিমে লেখক জানান, ‘এই সারমেয় শাসন ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।’
আজ, ২০২০ সালের সর্বাত্মক ও দুঃস্বপ্নতুল্য করোনা-সংক্রমণ আমাদের স্বার্থকে আবারও এক করে ফেলল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দীর্ঘজীবন কামনা করি, ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম নিশ্চয়ই আজকের দিনগুলি নিয়ে লেখা বাংলাভাষী আখ্যান পড়বে এবং একই রকম শিহরিত হবে।
(লেখকদের ব্যবহৃত পুরোনো বানান অপরিবর্তিত। )
Powered by Froala Editor