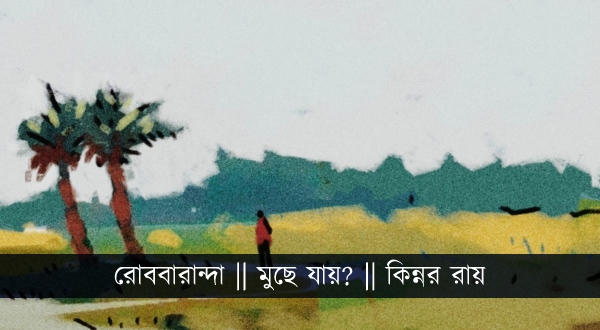মুছে যায়? — ৫৮
আগের পর্বে
তাল বাঙালির জীবনে নানা ধরনের খাবারের উপমা ও মাধ্যম হিসাবে হাজির হয়েছে। গো-বলয়ে, অখণ্ড বিহার, উত্তরপ্রদেশের ইলাহাবাদ, বারাণসী, লখনউতেও রমরমা তালের। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে তালের তাড়ির বিপুল রমরমা। বাংলার দুই পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুরে রয়েছে বড়ো বড়ো তাড়ির ঠেক। একসময় তাড়িবার ছিল কলকাতাতেও। তবে গো-বলয়ে তালক্ষীর, তালের বড়া তৈরির পদ্ধতি জানেন না সাধারণ মানুষ। তালগাছে বাসা বাঁধত বাবুইপাখি। সেই বাসা এক দশক আগেও বিক্রি হত বাংলার বিভিন্ন মেলায়। পরে রেপ্লিকা বেরনোর পর বিক্রি হত নকল বাবুইবাসা। তারপর...
‘তাল ঢ্যাঙা’— এই শব্দটা বাংলায় খুব প্রচলিত, মানে চালু— বিশেষ করে এই বঙ্গে— অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে। খুব লম্বা লোককে, স্বাভাবিকের থেকে খানিকটা বেশি লম্বা হলে, তখন সে ‘তাল ঢ্যাঙা’ বিশেষণ পেয়ে যেতে পারে। যেমন সত্যজিৎ রায়, যেমন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, যেমন ঋত্বিকদা— ঋত্বিককুমার ঘটক, যেমন ফেলুদা বা টেনিদা— চরিত্র হিসাবে।
আমি শুনেছি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নাকি সবাইকেই ‘তুমি’ বলতেন। মানে ‘তুমি’ সম্বোধন করতেন। ‘আপনি’র বালাই নেই। একবার নাকি তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেলিফোনে সুভাষণে সম্বোধন করে বলেছিলেন, শুনছি তাড়োশঙ্কর, তোমার কি সব লেকা নিয়ে তাতার ঢ্যাঙা ছেলেটা বায়োস্কোপ বানাচ্চে। তা টাকা দিয়েছে আমার সরকার।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তো পশ্চিমবঙ্গের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছ থেকে এই সুভাষিতাবলী টেলিফোন মারফত পেয়ে যারপরনাই স্তম্ভিত একেবারে। সত্যজিৎ-জননী, সুপ্রভা সায় ব্রহ্মসমাজ সূত্রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। তিনিও খানিকটা তদবির করেছিলেন তাঁর স্নেহ-আদরের মানিক যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী নিয়ে সিনেমা করার টাকা পায়। আসলে বিধানচন্দ্রের মুখে ‘তাতার ঢ্যাঙা ছেলেটা’ এই সম্ভাষণ, ‘ঢ্যাঙা’ শব্দটিকে যে জায়গায় নিয়ে যায়, তার আর নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। ‘তাল ঢ্যাঙা’ শব্দটিও আর ব্যাখ্যা কল্পের অবকাশ রাখে না।
তবে এই যে মুখগল্প বা মুখ-গল্প, তার তো আবার বহু ধরনের ব্যাখ্যা। সেই সময়ের কেউ কেউ বলে থাকেন, এটা মোটেই টেলিফোনিক সংলাপ ছিল না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনায়াসে তাড়োশঙ্কর হয়ে গেছেন। আর সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন জাতীয় কংগ্রেস দলের মনোনীত এমএলসি। পশ্চিমবঙ্গে তখন আপার ও লোয়ার হাউস বলতে বিধান পরিষদ ও বিধানসভা। বিধান পরিষদ আপার হাউস, বিধানসভা বা এসেম্বলি লোয়ার হাউস।
আরও পড়ুন
তাল বিলাইয়া তাল খাইও…
জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় মনোনীত এমএলসি-রা ছিলেন, বিধান পরিষদে। মূলত ক্ষমতাবান বড়ো জোতদার, বড়ো জমিদারেরা হতেন এমএলসি— মনোনীত বিধান পরিষদ সদস্য। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এলে তারা বিধান পরিষদ এবং এমএলসি পদ খারিজ করে। বহু বছর পর ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে জিতে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে বিধান পরিষদ ও এমএলসি পদ ফিরিয়ে আনেন।
আরও পড়ুন
ঘুড়ি তো জানে না সে নিজে ওড়ে না
যাক সে সব প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অসম্ভব বড়ো লেখক, অবশ্যই নোবেল পুরস্কারের দাবিদার লাভপুরের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকি বলেছিলেন, হ্যাঁ বাবা তাড়োশঙ্কর, তুমি আমাকে কিচু জানালে না, তাতার ঢ্যাঙা ছেলেটা বায়োস্কোপ বানাচ্চে তোমার বই নিয়ে।
আরও পড়ুন
কার ঘুড়িতে যে রেখেছি মন সোনা করে
প্রবল অভিমানী, আত্মাভিমানী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন তারাশঙ্কর নাকি এই কথার কোনো জবাবই দেননি। চুপই করেছিলেন। গল্প, গপ্পো হয়ে, কথায় হাঁটে। সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না। আর দায়ও নেই আমার। তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক বা ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়। শোনা যায় ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় তাঁর মন্ত্রিসভার সমস্ত মন্ত্রীদেরই নাকি রাইটার্স বিল্ডিংস মহাকরণে ঢুকে, কচ্ছপকে যেমন উল্টে দিলে তার গতি নড়াচড়া, সব স্তব্ধ হয়ে যায়, সেভাবেই তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের উল্টে দিতেন। যাতে তাঁরা কোনো কথাবার্তা না বলতে পারে। সে পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জি, খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মৎস্যমন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর অথবা ঈশ্বর দাস জালান— যেই হোন না কেন! সকলেই নাকি বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে ওলটানো কচ্ছপ।
আরও পড়ুন
ও, ও, ঘুড়ি— ঘুড়ি রে
এসব কথাও শোণা কথা। বহতা কথা। তাতা অর্থে সুকুমার রায়। তিনি তখন কালাজ্বরে প্রয়াত। সুপ্রভা রায় ছেলের সিনেমা নির্মাণের ব্যাপারে আগ্রহী। তাই তাঁর সরকারি অর্থ সাহায্যের জন্য তদবির, বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে।
বিধানচন্দ্র নাকি ‘পথের পাঁচালী’ নামে যুগান্তকারী লেখা ও সিনেমাটি নিয়ে এভাবেই বলতে চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে, অথবা সবই ‘গল্পের গরু’, কখন যে তারা চার পায়ে গাছে ওঠে আর ক-অ-খ-ন যে তারা নিচে— ভূমিতে নেমে আসে, তা বলা বড়োই কঠিন।
তবে সত্যজিৎ রায়কে নাকি ‘পথের পাঁচালী’ নামে যুগান্তকারী সিনেমার শেষে সদ্য স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত ‘উন্নতি’— শিল্পকারখানা, বাঁধ ইত্যাদির ছবি নাকি জুড়ে দিতে বলা হয়েছিল। সঙ্গে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, অন্য অন্য উন্নতির চিহ্ন, ছবি। যেমন নিউজরিল হয়— সরকারি সিনে প্রচার।
আমরাও দেখেছি এই সিনে প্রচার ছবি, পাড়ায় পাড়ায়, গ্রাম, শহর, শহরতলিতে। রাতের বেলা। সরকারি লোকজন, সাদা বড়ো— চৌকো পর্দা। তাতে সরকারি উন্নয়ন ছবি। হাসি মুখের ফসল ফলানো চাষি, কারখানার স্বাস্থ্যবান শ্রমিক। সেটা ১৯৬০ থেকেই প্রায়, মনে আছে। সোভিয়েত মডেলের বড়ো, বড়ো বাঁধ, মুখে মুখে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা— পাঁচ সালা পরিকল্পনার জয়-জয়কার তখন। তারপরই ১৯৬২-তে চিন-ভারত যুদ্ধ, খুবই দুঃখজনক সীমান্ত সংঘর্ষ। চিনা রেড আর্মি— পিএলএ নেমে এল আসামের তেজপুর পর্যন্ত, তারপর ফিরেও গেল আবার। তখন ‘বমডিলার পতন’ এই হেডলাইনটা খুব দেখতাম বাংলা দৈনিকে, মানে বমডিলা চিনা লালফৌজ দখল নেওয়ার পর। নেফা, লাদাখের কথা ১৯৬২-তে খুবই উচ্চারিত হত বেতারে— রেডিওতে। ‘আকাশবাণী’র খবরে নেফা, লাদাখ, বমডিলা। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি দৈনিকেও এইসব নাম বার বার ফুটে ওঠে। যাক সেসব কথা। ১৯৬২-র চিন-যুদ্ধের পর শহর, শহরতলি, গ্রামে যে সরকারি প্রচার-ছবি দেখানো হত, তা পাবলিকের মুখে মুখে কেমন করে যেন হয়ে গেল ওয়ার পিকচার। আর সেই ওয়ার পিকচার দেখার জন্য নানা বয়সের মানুষ। ছেলেমেয়ে, মাঝ বয়স, আধ বয়স, বুড়ো-বুড়ি, সবাই। সাধারণত সন্ধে লেগে যাওয়ার পর বসন্তকালীন পৃথিবীতে সেই সান্ধ্য ওয়ারপিকচার। সেখানে ছুটে বেড়ানো বাতকম্মের দুর্বিষহ দুর্গন্ধ, বিড়ির গন্ধ, নানা রকম শব্দ। সব মিলিয়ে যাকে বলা যায় এক নৈনিত্তর অবস্থা। সেই ওয়ার পিকচারের নিয়মিত দর্শক ছিলাম। বালি স্কুল মাঠ— বাড়ি থেকে অনেক দূর, গঙ্গা, পাঠকঘাট, পাঠকঘাট শ্মশানের পাশে— শান্তিরাম বয়েজ স্কুল আর গঙ্গার গায়ে, বালি স্কুল মাঠ বা বালি এসি মাঠ। বালি এসি— বালি অ্যাথলেটিক ক্লাব। সেখানে নিয়মিত ফুটবল। ফুটবল আর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। খুব কাছেই বালি সাধারণ গ্রন্থাগার— বালি পাবলিক লাইব্রেরি, বালি মিউনিসিপ্যালিটি— সবই বহু বছরের পুরনো। তো সেই বালি স্কুল মাঠেই ওয়ার পিকচার দেখানোর আয়োজন। বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়— আমাদের স্কুলের সামনে ফাঁকা জমিতে ওয়ার পিকচার দেখানোর আয়োজন, রাতে। সেখানেও চিলিবিলি ভিড়। এই মাঠেই ১৯৬২ সালে খোঁড়া হয়েছিল পরিখা বা ট্রেঞ্চ, বোমা ফেলার জন্য চিনা যুদ্ধ বিমান হানা দিলেই সেখানে যাতে আম পাবলিক লুকিয়ে পড়তে পারে। সেই সময়েই জহর+বাণী এমন অক্ষরমালা ফুটে উঠত বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয় লাগোয়া বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে। কারা যে লিখত এসব। রূপবান জহর আর তাদের দোতলা বাড়ির উল্টোদিকে রূপময়ী বাণী। তাদের বাড়িও দোতলা। জহর টেন, বাণী নাইন। জহর বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী। বাণী বালি বঙ্গ শিশু বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস নাইন। জহরের চোখের মণি মার্জার সদৃশ আর বাণীর চোখের মণি কালো। বাণীর আর এক দিদি বা বোন ছিল, প্রায় একই রকম দেখতে।
জহর ফর্সা, বাণীও। তখন বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের প্রবোধভবন— বারি তৈরি হয়নি। সেই ফাঁকা মাঠে ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ। স্কুলের স্পোর্টস দু-একবার। ক্রীড়া শিক্ষক বারীণদা বা গোপালবাবুর পরিচালনায় হকি খেলা। সেই মাঠেই ঘুড়ির হররা— সরস্বতী পুজোর সময়। বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ— প্যান্ডেল বেঁধে, বেশ কয়েকবার। বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এসেছিলেন একবার এই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমানিতে— পারিতোষিক বিতরণ সভায়। এই সভায় স্কুল থেকে পাওয়া পুরস্কারের আলাদা গল্প আছে, আমার সত্যেন্দ্রনাথ বসুর হাত থেকে পুরস্কার পাওয়ার কাহিনি, সেই গল্প সামনের কোনো ‘মুছে যায়?’-তে বলব।
এ তো গেল ওয়ার পিকচারের কথা। এবার আসি ঢ্যাঙা প্রসঙ্গে। আবার! বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ের থেকে সামান্য দূরেই ঢ্যাঙা পুকুর। ভট্টাচার্যদের— ভচ্চায্যিদের শরিকানি পুকুরের উল্টো দিকেই ঢ্যাঙা পুকুর। দুই পুকুরের মাঝখান দিয়ে মাটির উঁচু রাস্তা। বালি বাজারে, বাস থেকে নেমে সোজা গোঁসাই পাড়া বা গোস্বামী পাড়া রোড ধরে জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়-এর দিকে যেতে গেলে বাঁ দিকে পড়বে ঢ্যাঙা পুকুর। পাকা রাস্তা থেকে নেমে একটু ভেতরে— নানা, ‘ভেতর’ বলতে দু পা গেলেই ভচচায্যিদের শরিকি পুকুর, যেখানে ঘাট সরে সবাই আর ঢ্যাঙা পুকুর। দুই পুকুরে যোগাযোগের জন্য বড়োসড় সিমেন্টের পাইপ আছে। তা দিয়ে জল আসা-যাওয়া করতে পারে কিন্তু মাছ নয়, কুঁচে বা ঢোঁড়া সাপ বা পানি কেউটেও নয়, কারণ এই পাইপ বা বড়োসড় নলের— দু দিকেই জাল। ভচচায্যিদের পুকুর, ঢ্যাঙা পুকুর— সবই বার্ষিক টাকার হিসাবে জমা নেন কৃশকায়, কুঞ্চিত কেশ, কৃষ্ণবর্ণ একজন। তিনি নিজে জাল ফেলে মাছ ধরেন। সে এক দেখার ব্যাপার। তাঁদের জালে গেঁড়ি, গুগলি, পুকুরের ঝিনুক— যা ঘষে ঘষে বড়ো ফুটো তৈরি করে শশা, কাঁচা আমের খোসা ছাড়ানো হয়, সেই ঝিনুক আজকাল, আজকাল কেন বহু বছরই দেখি না, তো সে যাই হোক, তাঁর জালে কুঁচে, জলঢোঁড়া, এমনকি পানি কেউটেও আটকায় এক একবার। পানি কেউটে থাকে জলে। তাকে মেছো কেউটেও বলেন কেউ কেউ। এই পুকুর জমা নেওয়া জনের নাম ছিল কি বঙ্কু? আজ আর মনে নেই।
দুই পুকুরের মাঝে মাটিতে তৈরি উঁচু রাস্তায় এক জোড়া পুরষ্টু, প্রাচীন তালগাছ। কি চমৎকার সেই গাছে ফলা তালেদের সোয়াদ। ভাদ্রমাসে ধুপধাপ তাল পড়ে ঢ্যাঙা পুকুরে। নাপতে— নাপিত বাড়ির হাবি, সুনীল, অনিলা— মুহূর্তে সাঁতরে তাল ধরে নিয়ে যায়। বড়ো, পাকা, পুরুষ্টু তাল। কালো, গাছপাকা তালে দারুণ ক্ষীর, বড়া। লালচে নয়, কালো তালেই চমৎকার ফুলুরি, ক্ষীর। নাপিত বাড়ির অনিলা আমার থেকে খানিকটা বড়ো। ফর্সা, বড়ো বড়ো চোখ। সেটা ১৯৬২ সালটাল হবে। অনিলা তার ফ্রকের নিচটুকু জলে ভাসিয়ে সাঁতার দেয়। আমি তাকে বলি, অনিলে— কিলকিলিলে— কেন বলি, কে জানে। সে আমায় বলে, খোকা। খোকা।
বালি বাজারে ভাদ্রমাসে— সিজনে একটা বড়ো তাল দশ নয়া পয়সা থেকে পঁচিশ নয় পয়সা। জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসবে তালের দাম বাড়ে স্বাভাবিকতায়। এখন একটা ভালো, পাকা তাল ব্রহ্মপুর বাজের পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা। জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসবে তার দর বেড়ে হয় পঞ্চাশ টাকা। একটা তাল পঞ্চাশ টাকা।
অনিলা এসে মাঝে মাঝে তাল দিয়ে যেত মা-কে, কোনো দাম না নিয়েই। পাকা তালের আঁটি মাটিতে ফেললে ধীরে, সুস্থে তালফোঁপর। লক্ষ্মী পুজো— কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় সেই তাল আঁটিতে ফোঁপর হয়ে গেলে, তাকে কাটারি দিয়ে কেটে পুজোর থালায়— নৈবেদ্যর পাশে। তাল ‘চাঁচা’ বা ‘গোলা’র সময় যে নুটি বেরয়, তাও চুষে খাওয়া হত আমাদের বালকবেলায়।
আগেই বলেছি, গোবলয়ে বা হিন্দিবলয়ে কাঁচা তাল খাওয়ার ব্যাপার সামান্য থাকলেও বড়া, ক্ষীর বা ফুলুরি বানিয়ে খাওয়ার কোনো চলই নেই। অথচ শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপুজোয় আস্ত তাল অবধারিত, বরিশালে। ভট্টচার্যদের পুকুর আর ঢ্যাঙা পুকুরের মাঝে যে পায়ে চলা উঁচু, মাটির রাস্তা, সেখানে গরমে বুকে হাঁটা দুই প্রাচীন অথবা অতি প্রাচীন খড়িশ। সন্ধ্যায় তাঁরা হাওয়া খেতে নয়তো ব্যাঙ ধরতে বেরোন। তখন বালিতে কত কত ব্যাঙের ডাক। কোলা ব্যাঙ, যা মুরগির ঠ্যাঙকেও হার মানিয়ে দেয়। রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় কোলা নয়, সোনা ব্যাঙের ঠ্যাঙ। ষাট দশকেই গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক সোনা ব্যাঙ ধরা শুরু হয়, বিদেশে চালান দেওয়ার জন্য। বর্ষার রাতে তিন ব্যাটারি বা দু ব্যাটারির বড়ো বড়ো টর্চ জ্বেলে লোহার পোক্ত চিমটে আর চটের ব্যাগ নিয়ে সোনা ব্যাঙ শিকারিরা। এভাবেই সোনা ব্যাঙ প্রায় প্রজাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সাপে ব্যাঙ ধরলে ব্যাঙের গলা থেকে করুন এক মরণ-ডাক বেরিয়ে আসে। দীর্ঘ— একটানা। যেমন ঝিঁঝিঁ ডাকে। আজকাল তো শহরে, ঝিঁঝিঁও ডাকে না। জোনাকিরা নিরুদ্দেশ কবেই। পাখ-পাখালি প্রায় নেই।
তো সেই জোড়া খরিশ তাল থাকতেন তাল গাছের কাছেই, জলার পাশে। তখন বালিতে ইলেকট্রিক আসেনি। সেটা ১৯৫৯-৬০ সাল। সাধারণ মানুষ অন্ধকারেই পথ হাঁটেন। বালিতে তখন কলের জল আসেনি— রাস্তার ট্যাপ কল। বিমল মান্না নামে একজন নির্বাচিত পুরপিতা ছিলেন বালি মিউনিসিপ্যালিটির। তিনি বামপন্থী কাউন্সিলর, দাঁড়াতেন পাকা বাড়ি চিহ্ন নিয়ে। বড়ো ওয়ালক্লক— সেই ঘড়িকে নির্বাচনী প্রতীক করে ভোটে দাঁড়াতেন জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীরা। ইন্দুভূষণ ব্যানার্জি নামে একজন ভোটে জেতা জাতীয় কংগ্রেস কাউন্সিলর ছিলেন বালি মিউনিসিপ্যালিটিতে, সেটা ষাট দশকের কথা। বিমল মান্নাও তাই। ইন্দুভূষণবাবু খুব ক্রীড়া প্রেমী ছিলেন— স্পোর্টস লাভার। বালি ইয়ং অ্যাসোসিয়েশান, বালি এসি ক্লাব, কামারপাড়ার শিশু সমিতি, নবীন সংঘ, তরুণ সংঘ— সব ক্লাবেই ছিল ইন্দুভূষণ ব্যানার্জির কম-বেশি প্রভাব।
Powered by Froala Editor